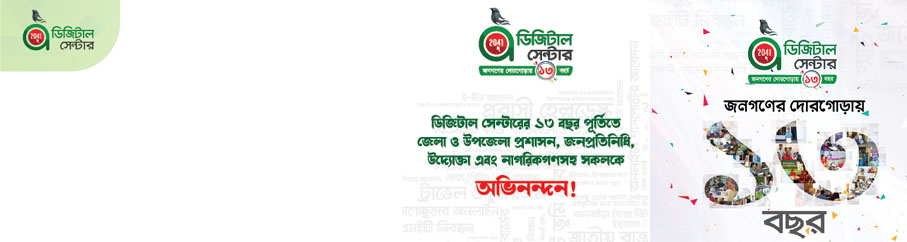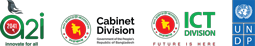-
প্রথম পাতা
- ইউনিয়ন সর্ম্পকিত
- ইউনিয়ন পরিষদ
- সরকারি অফিস
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
-
🎓 সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
-
🎓 খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
-
🎓 রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়
-
🎓 সুন্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
-
🎓 এস.পি.কে দাখিল মাদ্রাসা
-
🎓 খালিশপুর দাখিল মাদরাসা
-
🎓 বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খর্দ্দ খালিশপুর
-
🎓 খালিশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 বজরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 ভালাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 শাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 মোঃ আজমত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 কাকিলাদাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ
-
🎓 সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
- বিভিন্ন তালিকা
- প্রকল্প
-
সেবা সমূহ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
-
কী কী সেবা পাবেন
-
পুরুষ উদ্যোক্তা প্রোফাইল-১
-
নারী উদ্যোক্তা প্রোফাইল-২
-
সেবার মূল্য তালিকা
-
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার
-
সর্বজনীন পেনশন রেজিস্ট্রেশন
-
ই-জাতীয় পরিচয় পত্র
-
ই-পাসপোর্ট
-
ই-পুলিশ ক্লিয়ারেন্স
-
এ- চালান
-
ই-নামজারি
-
এমআইএস আবেদন
-
বৈদ্যুতিক মিটারের আবেদন
-
ই-ট্রেন টিকিট
-
বিমান ই-টিকিট
-
ব্যাংক এশিয়া
-
টিসিবি'র অনলাইন সেবা
-
আমার সরকার
-
বিবাহ রেজিষ্টার
-
প্রবাসী হেল্পডেস্ক
-
কী কী সেবা পাবেন
- গ্যালারি
- যোগাযোগর ব্যবস্থা
-
প্রথম পাতা
-
ইউনিয়ন সর্ম্পকিত
ইউনিয়ন পরিচিত
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
অন্যান্য
এস.বি.কে এর ইতিহাস
-
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম
গ্রাম আদালত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অফিস পরিদর্শন
-
সরকারি অফিস
ভূমি
স্বাস্থ্য সেবা
৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- 🎓 সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
- 🎓 খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- 🎓 রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- 🎓 সুন্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- 🎓 এস.পি.কে দাখিল মাদ্রাসা
- 🎓 খালিশপুর দাখিল মাদরাসা
- 🎓 বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খর্দ্দ খালিশপুর
- 🎓 খালিশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 বজরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 ভালাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 শাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 মোঃ আজমত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 কাকিলাদাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
-
বিভিন্ন তালিকা
সুবিধাভোগীদের তালিকা
অন্যান্য তালিকা
- প্রকল্প
-
সেবা সমূহ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
- কী কী সেবা পাবেন
- পুরুষ উদ্যোক্তা প্রোফাইল-১
- নারী উদ্যোক্তা প্রোফাইল-২
- সেবার মূল্য তালিকা
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার
- সর্বজনীন পেনশন রেজিস্ট্রেশন
- ই-জাতীয় পরিচয় পত্র
- ই-পাসপোর্ট
- ই-পুলিশ ক্লিয়ারেন্স
- এ- চালান
- ই-নামজারি
- এমআইএস আবেদন
- বৈদ্যুতিক মিটারের আবেদন
- ই-ট্রেন টিকিট
- বিমান ই-টিকিট
- ব্যাংক এশিয়া
- টিসিবি'র অনলাইন সেবা
- আমার সরকার
- বিবাহ রেজিষ্টার
- প্রবাসী হেল্পডেস্ক
জাতীয় ই-সেবা
-
গ্যালারি
ফটো গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
-
যোগাযোগর ব্যবস্থা
অফিস যোগাযোগ
যোগাযোগ ম্যাপ
"গ্রাম আদালত আইন" বলতে বাংলাদেশে কার্যকর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে ন্যায়বিচার সহজলভ্য করা হয়েছে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো—গ্রাম পর্যায়ে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ দ্রুত, কম খরচে ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিষ্পত্তি করা।
বাংলাদেশে বর্তমানে যেটি কার্যকর, সেটি হলো:
গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (Village Court Act, 2006)
এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য:
গ্রাম আদালতের গঠন:
ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়নে একটি গ্রাম আদালত গঠিত হয়।
এতে মোট ৫ জন সদস্য থাকেন:
১ জন চেয়ারম্যান (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান),
বাদী ও বিবাদীর মনোনীত ৪ জন সদস্য (দুই পক্ষের মধ্যে সমান সংখ্যায়)।
বিচারযোগ্য মামলা:
গ্রাম আদালত সাধারণত এমন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা শুনতে পারে যেগুলোর আর্থিক মূল্য বা ক্ষতিপূরণ সীমিত (প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত, সংশোধনী অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে)।
সাধারণ ঝগড়া, হালকা মারামারি, হুমকি, সামান্য চুরির মতো বিষয়াদি এতে পড়ে।
আপিল ও কার্যপ্রণালী:
গ্রাম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ সীমিত।
কার্যপ্রণালী সরল, দাপ্তরিকতা কম এবং গ্রাম্য প্রেক্ষাপটে উপযোগী করে তৈরি।
আইনটির উদ্দেশ্য:
গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পমূল্যে, দ্রুত ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করা।
থানা ও আদালতের উপর চাপ কমানো।
সংশোধন:
২০০৬ সালের আইনের পরবর্তীতে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে, যেমন:
গ্রাম আদালত আইন (সংশোধন) ২০১৩
Village Courts (Amendment) Act, 2023
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস