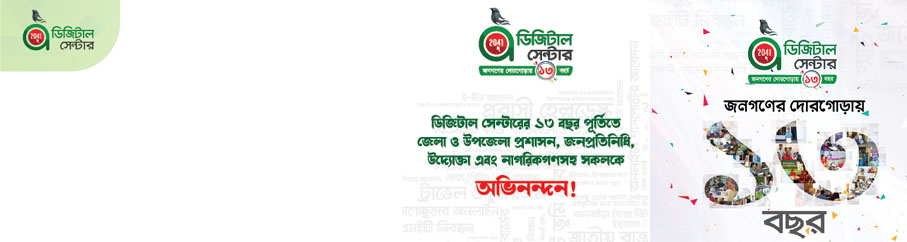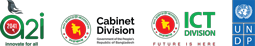-
প্রথম পাতা
- ইউনিয়ন সর্ম্পকিত
- ইউনিয়ন পরিষদ
- সরকারি অফিস
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
-
🎓 সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
-
🎓 খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
-
🎓 রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়
-
🎓 সুন্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
-
🎓 এস.পি.কে দাখিল মাদ্রাসা
-
🎓 খালিশপুর দাখিল মাদরাসা
-
🎓 বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খর্দ্দ খালিশপুর
-
🎓 খালিশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 বজরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 ভালাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 শাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 মোঃ আজমত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 কাকিলাদাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
-
🎓 সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ
-
🎓 সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
- বিভিন্ন তালিকা
- প্রকল্প
-
সেবা সমূহ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
-
কী কী সেবা পাবেন
-
পুরুষ উদ্যোক্তা প্রোফাইল-১
-
নারী উদ্যোক্তা প্রোফাইল-২
-
সেবার মূল্য তালিকা
-
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার
-
সর্বজনীন পেনশন রেজিস্ট্রেশন
-
ই-জাতীয় পরিচয় পত্র
-
ই-পাসপোর্ট
-
ই-পুলিশ ক্লিয়ারেন্স
-
এ- চালান
-
ই-নামজারি
-
এমআইএস আবেদন
-
বৈদ্যুতিক মিটারের আবেদন
-
ই-ট্রেন টিকিট
-
বিমান ই-টিকিট
-
ব্যাংক এশিয়া
-
টিসিবি'র অনলাইন সেবা
-
আমার সরকার
-
বিবাহ রেজিষ্টার
-
প্রবাসী হেল্পডেস্ক
-
কী কী সেবা পাবেন
- গ্যালারি
- যোগাযোগর ব্যবস্থা
-
প্রথম পাতা
-
ইউনিয়ন সর্ম্পকিত
ইউনিয়ন পরিচিত
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
অন্যান্য
এস.বি.কে এর ইতিহাস
-
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম
গ্রাম আদালত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অফিস পরিদর্শন
-
সরকারি অফিস
ভূমি
স্বাস্থ্য সেবা
৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- 🎓 সরকারি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান ডিগ্রি কলেজ
- 🎓 খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- 🎓 রাহাতুল্লাহ সরদার মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- 🎓 সুন্দরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- 🎓 এস.পি.কে দাখিল মাদ্রাসা
- 🎓 খালিশপুর দাখিল মাদরাসা
- 🎓 বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ হামিদুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খর্দ্দ খালিশপুর
- 🎓 খালিশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 বজরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 ভালাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 শাহাবাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 সুন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 মোঃ আজমত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 কাকিলাদাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- 🎓 সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
-
বিভিন্ন তালিকা
সুবিধাভোগীদের তালিকা
অন্যান্য তালিকা
- প্রকল্প
-
সেবা সমূহ
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
- কী কী সেবা পাবেন
- পুরুষ উদ্যোক্তা প্রোফাইল-১
- নারী উদ্যোক্তা প্রোফাইল-২
- সেবার মূল্য তালিকা
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার
- সর্বজনীন পেনশন রেজিস্ট্রেশন
- ই-জাতীয় পরিচয় পত্র
- ই-পাসপোর্ট
- ই-পুলিশ ক্লিয়ারেন্স
- এ- চালান
- ই-নামজারি
- এমআইএস আবেদন
- বৈদ্যুতিক মিটারের আবেদন
- ই-ট্রেন টিকিট
- বিমান ই-টিকিট
- ব্যাংক এশিয়া
- টিসিবি'র অনলাইন সেবা
- আমার সরকার
- বিবাহ রেজিষ্টার
- প্রবাসী হেল্পডেস্ক
জাতীয় ই-সেবা
-
গ্যালারি
ফটো গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
-
যোগাযোগর ব্যবস্থা
অফিস যোগাযোগ
যোগাযোগ ম্যাপ
ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী
ভূমিকা
বাংলাদেশের গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি)। এটি জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী সরকারী প্রতিষ্ঠান, যা স্থানীয় উন্নয়ন, প্রশাসন, এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সাফল্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও টেকসই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য।
ইউনিয়ন পরিষদের ইতিহাস
বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সূচনা হয় ঔপনিবেশিক আমলে। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে, ১৯৫৯ সালের "বেসিক ডেমোক্রেসি অর্ডিন্যান্স"-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো সুসংহত হয়। স্বাধীনতার পর সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা ও ক্ষমতায়ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে, এটি স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।
গঠন ও কাঠামো
প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়:
১ জন চেয়ারম্যান
৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন সাধারণ সদস্য
৩টি সংরক্ষিত নারী সদস্য (প্রতিটি ৩টি ওয়ার্ডের জন্য একজন)
সদস্য ও চেয়ারম্যান সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন, এবং তাদের মেয়াদ ৫ বছর।
ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যাবলী
১. প্রশাসনিক কার্যাবলী
নাগরিক সনদপত্র, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রদান
ভৌগোলিক সীমানার সংরক্ষণ ও পরিবর্তনের প্রস্তাবনা
স্থানীয় জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
২. বিচারিক কার্যাবলী (সালিশি ভূমিকা)
প্রাথমিকভাবে পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা
ইউনিয়ন বিচার বোর্ডের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
৩. উন্নয়নমূলক কার্যাবলী
গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: সড়ক, ব্রিজ, বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে সহায়তা প্রদান
ইউনিয়ন পর্যায়ে বাজার (হাট-বাজার) উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা
৪. আর্থিক কার্যাবলী
ইউনিয়ন কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) আদায়
বাজার ফি, জলমহাল ইজারা ফি ইত্যাদি রাজস্ব আদায়
সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার
৫. সামাজিক সেবা ও নিরাপত্তা কার্যক্রম
বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণ
খাদ্য সহায়তা, ভিজিডি, ভিজিএফ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন
শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
দুর্যোগ প্রস্তুতি, আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা
দুর্যোগকালীন ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম
নদী ভাঙন, বন্যা ইত্যাদির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা
৭. পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যাবলী
বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম
টেকসই কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা
ইউনিয়ন পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ
অর্থনৈতিক দুর্বলতা: প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ থাকে।
দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাব: কিছু ক্ষেত্রে হিসাবের স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয় না।
প্রশিক্ষণের অভাব: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পর্যাপ্ত প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।
জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি: জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ অনেক সময় কম লক্ষ্য করা যায়।
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: দলীয় স্বার্থের কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।
সমাধানের পথ
পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ: সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং নিজস্ব আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ।
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: অনলাইন সেবা চালু ও তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা।
জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি: গ্রাম আদালত ও সামাজিক কমিটির মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো।
উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার: ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন সনদ প্রদান ইত্যাদি আধুনিক সেবা চালু করা।
উপসংহার
ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দেশের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ হতে পারে প্রকৃত অর্থে "জনগণের সরকার"।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস